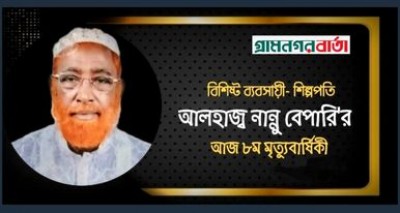বর্ষার সেই দিনগুলোতে
 মহিউদ্দিন খান মোহন
মহিউদ্দিন খান মোহন
প্রকাশ: ২০ জুন ২০২১, ১১:০৮ | আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ০২:৩৬

মেঘের গুরুম গুরুম ডাকে ঘুম ভাঙলো । কোথাও একটা বাজও পড়ল মনে হলো। একটু পরেই ঝম ঝম করে নামল বৃষ্টি। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল দিনটি পহেলা আষাঢ়। বাংলা ঋতুচক্রের দ্বিতীয় ঋতু বর্ষাকালের প্রথম দিন। ষড় ঋতুর এই বাংলাদেশে বর্ষা দখল করে আছে এক অনন্য স্থান। বর্ষাকে উপজীব্য করে প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিকরা রচনা করে গেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস গান। বাঙালির কাছে বর্ষা এক অত্যন্ত প্রিয় ঋতু। এই বর্ষা আরো বাঙ্ময় হয়ে ওঠে কবিদের কবিতা-গানে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি’, ‘আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে’ কিংবা ‘বাদল দিনের প্রথম কদমফুল করেছ দান..’ গানগুলো শুনলেই বর্ষাকালের মেঘমেদুর রোমান্টিকতা এই বয়সেও আমাকে আপ্লুত করে, নিজের অজান্তেই মনকে করে তোলা উতলা। মন ফিরে যেতে চায় পাঁচ দশক পেছনে ফেলে আসা সেই সুন্দর দিনগুলোতে। শুধু আমি কেন, যে কাউকে তা সোনালী অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বলে আমার বিশ্বাস।
স্কুলছাত্র অবস্থায় আমাদেরকে পড়তে হয়েছে ‘বর্ষাকাল’ শিরোনামের প্রবন্ধ। তাতে আমরা অজ্ঞাত কোনো লেখকের লেখা বর্ষাকালের বিবরণ মুখস্থ করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করেছি। তখন বুঝিনি বইয়ে বর্ণিত বর্ষার রূপের চেয়ে এর প্রকৃত রূপ কত সুন্দর, কত মোহময়! সে বয়সে বর্ষার রূপ-সৌন্দর্যের সুধা পান করার মতো আবেগ-অনুভ‚তি হৃদয়-মগজে বাসা বাঁধেনি। বেঁধেছে আরো পড়ে, যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছি। পরবর্তীতে বর্ষার যে রূপ স্বচক্ষে দেখেছি, তা কখনোই ভুলে যাবার মতো নয়। যৌবনে বর্ষাকে নিয়ে ভাবালুতায় আক্রান্ত হন নি এমন মানুষ এপার বাংলা-ওপার বাংলায় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমাদের এ অ লে যে ছয়টি ঋতু আছে, সেগুলোর মধ্যে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এবং বসন্ত মানুষকে যতটা আমোদিত করে, অন্য দুটি তেমন পারে না। তবে, নগর জীবনে গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীতের উপস্থিতি অনুভব করা গেলেও বাকিগুলোর আগমন-প্রস্থান টেরই পাওয়া যায় না।
জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাটিয়েছি গ্রামে। গ্রামের কাদামাটি গায়ে মেখে, খালের স্বচ্ছ পানিতে অবগাহন করে আমাদের বেড়ে ওঠা। বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্রের স্বাদ আমরা তাই বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করেছি। গ্রীষ্মে যেমন তীব্র গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছি, তালপাতার পাখার বাতাসে শরীর জুড়ানোর চেষ্টা করেছি, কিংবা কোনো গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছি একটু স্বস্তির আশায়, তেমনি প্রচন্ড শীতে লেপকাঁথার নিচে গুটিসুটি মেরে পার করেছি রাত। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে ফুটবল খেলায় মেতে ওঠার স্মৃতি হয়তো অনেকেরই আছে। শীত পেরিয়ে গেলেই মৃদুমন্দ দখিনা হাওয়া বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে বইতে শুরু করত। শরতের পূর্ণিমারাতে নির্মেঘ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের আলোর বন্যার সৌন্দর্য যে উপভোগ করেনি, তার মতো দুর্ভাগা আমার বিবেচনায় কমই আছে। আর হেমন্তের সকালে ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু শিশিরের উপস্থিতি যেন ঘোষণা করত- শীত আসছে। এসব উপভোগ তারাই করেছেন, যারা জীবনের একটি সময় কাটিয়েছেন গ্রামবাংলায়। কংক্রিটের নগরজীবনে এসব সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ নেই।
কত সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো! আমি আমার স্মৃতির কথা বলতে পারি। বর্ষা এলইে আমরা গৃহবন্দী হয়ে যেতাম। গৃহবন্দী না বলে ‘বাড়িবন্দী’ বলাই বোধকরি যুক্তিযুক্ত। কেননা, চারদিকে পানির প্রাচীরঘেরা বাড়িই হয়ে যেত আমাদের বিচরণভ‚মি। আমাদের বিক্রমপুর অ লটি নিচু এলাকা। ভরা বর্ষায় এর মাঠ-ঘাট সব তলিয়ে যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ নাগাদ খাল-বিলে জোয়ার আসত। টইটুম্বুর হয়ে উঠত পুকুর-ডোবাগুলো। চৈত্রমাসে শুকিয়ে শীর্ণ নালায় পরিণত হওয়া খালগুলো ফিরে পেত যৌবন। আমাদের গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটি খাল বয়ে গেছে। যেটার নাম ‘যমদুয়ারি’ খাল। এই অদ্ভ‚ত নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। কে কবে এই খালে যমের জন্য দুয়ার খুলে দিয়েছিল তাও কেউ বলতে পারে না। যাহোক, শীতকালে এই খালের পানি কমতে কমতে হাঁটু মাপে নেমে আসত। আমরা গ্রামের এক দঙ্গল বালক-কিশোর হইহই করতে করতে সেখানে মাছ মারতাম। কিন্তু বর্ষা এলেই সেই যমদুয়ারি খাল কানায় কানায় ভরে উঠত। ভরাপেটের যমদুয়ারি অতিরিক্ত পানি উগড়ে দিত দু’পাশে। আর তাতে আমাদের খেলার মাঠ তলিয়ে যেত ছয় মাসের জন্য। আমাদের এলাকার বাড়িগুলো একটি থেকে আরেকটি দূরে দূরে। শুকনো মৌসুমে পায়ে হেঁটে এবাড়ি ওবাড়িতে যাতায়াত হয়। কিন্তু বর্ষা এলেই বাড়িগুলো একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখন অবশ্য রাস্তাঘাট হওয়ায় অনেক বাড়িই পরস্পর সংযুক্ত। তখন বাড়িগুলোকে কোনো বৃহৎ জলাশয়ে দ্বীপের মতো মনে হতো। আমরা শিশু-কিশোররা হতাম সেই বিছিন্ন দ্বীপের বন্দী। বিচরণ ক্ষেত্র ঘর আর উঠোন। তাও আবার কোনো কোনো বছর বন্যায় সেই উঠোনও তলিয়ে যেত। তখন ঘরের মধ্যে ‘আমি বন্দী কারাগারে, আছি গো মা বিপদে’ গানের অবস্থা।

আমাদের গ্রামের পশ্চিমাশ দিক দিয়ে বয়ে গেছে সিরাজখিান-শ্রীনগর-লৌহজং খাল। এটাকে আমরা বলতাম বড়খাল। খালটি উত্তরে সিরাজদিখান উপজেলার সৈয়দপুরে ধলেশ্বরী নদী ও দক্ষিণে লৌহজং উপজেলার দিঘলীর কাছে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কে কবে এটি খনন করিয়েছিলেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তার ‘বিক্রমপুরের ইতিহাস’ গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) এ খাল থেকে বিভিন্ন ছোটো ছোটো খালের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ঢাকার সঙ্গে রাজনগরের দূরত্ব কমানোর জন্য রাজা রাজবল্লভের পূত্র রাজা রামদাস দেওয়ান পদ্মা ও ধলেশ্বরীকে সংযুক্তকারী তালতলা খালটি খনন কথা করিয়েছিলেন। একই গ্রন্থে তিনি ‘হলদিয়ার খাল’ নামে যে খালের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটাই আমাদের বড়খাল। ধারণা করা হয়, এই খালটিও ওই সময়ে একই উদ্দেশ্যে খনন করা হয়েছিল। আমরা এ খালটিকে দেখেছি ছোটখাটো একটি নদীসম। শুকনো মৌসুমে এর পানি প্রবাহের ধারা কিছুটা কমে এলেও পণ্যবাহী গয়না নৌকা চলাচল করতে পারত। বর্ষাকালে এ খালটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করত। পদ্মা থেকে আসা পানিতে দু’পাশের মাঠ প্লাবিত হয়ে নদীতে পরিণত হতো । তখন এ খাল দিয়ে ষাট ফুট দৈর্ঘ্যরে ল ঢাকা-শ্রীনগর-গোয়ালীমান্দ্রা রুটে চলাচল করত। এখন সে খালের করুণদশা। ভরা বর্ষায়ও সে শীর্ণকায়। পলি পড়তে পড়তে এর বুক ভরাট হয়ে গেছে। এখন ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এর তলদেশে কিশোর-বালকরা ফুটবল খেলে। ১৯৭৯-৮০ সালে একবার খালটি পুনঃখনন করা হয়েছিল। তারপর আর কোনো সংস্কার হয়নি। যাহোক, বর্ষাকালে বড়খালের ভীষণদর্শন মূর্তি আমাদের হৃদকম্প সৃষ্টি করত।
ছেলেবেলায় দেখেছি আষাঢ় মাসের প্রথম সাতদিন খুব বৃষ্টি হতো। একরকম টানা বৃষ্টি। বয়স্কদের মুখে গল্প শুনতাম এক রাজার সাত মেয়ে ছিল। আষাঢ় মাসের প্রথম সাতদিনে তাদের বিয়ে হয়েছিল। বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে যাবার সময় সে রাজকন্যারা হাপুস নয়নে কেঁদেছিল। তাই প্রতি বছর আষাঢ় মাসের প্রথম সাতদিন এমন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়। গল্প শুনতে শুনতে সাত রাজকন্যার কষ্টে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করত। বড় হয়ে বুঝেছি ও কেবলই গল্প। বাস্তব নয়। সবই ঋতু বৈচিত্র্যের খেলা। তবুও আষাঢ় মাসের প্রথম দিনগুলোতে বৃষ্টি না হলে কেমন যেন শূন্যতা অনুভূত হয়। কী যেন বাকি থেকে গেল এমন একটা অনুভ‚তি। অমন বৃষ্টিতে আমরা খুশিই হতাম। কেননা, স্কুলে যাওয়া লাগত না। সারাদিন ঘরের মধ্যে হুটোপুটি। বৃষ্টির মধ্যে চাল আর কাঁঠালবিচি ভাঁজা খাওয়ার মজাই আলাদা। ঝুম বৃষ্টিতে যারা তা খাননি, তারা এর মজা অনুভব করতে পারবেন না।
তবে, প্রকৃতিতে যে একটা নীরব পরিবর্তন ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে অনেকেই তা লক্ষ্য করে থাকবেন। এই যেমন গত কয়েক বছর আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি হয়নি। খাঁ খাঁ রোদ ঘাম ঝরিয়েছে সবার। রসিকতা করে অনেকে তখন বলেছেন, রাজকন্যারা বোধহয় ‘কোর্ট ম্যারেজ’ করে ফেলেছে, তাই কান্নাকাটি নেই। তবে এবার পহেলা আষাঢ় সকালবেলাতেই যখন ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল, স্মৃতিতে ভেসে উঠল শৈশবের সেই উদ্দাম দিনগুলো। এমন বৃষ্টিতে মায়ের নিষেধাজ্ঞার থোড়াই কেয়ার করে এবং পরিনামে অনিবার্য ‘উত্তম মধ্যমের’ ঝুঁকি মাথায় নিয়েই দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তাম আমাদের যমদুয়ারি খালে। পানিতে ডুব দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার রিমঝিম শব্দের সঙ্গীত উপভোগ করা কী যে আনন্দের, তা বলে বোঝানো যাবে না। আজ আর সে সুযোগ নেই। সময় বড় নির্দয়। বয়স, পরিবেশ ও পরিস্থিতি সবকিছু বদলে দিয়েছে। তবে বাল্যকালের সে উদ্দাম দিনগুলোর স্মৃতি এখনও নষ্টালজিয়ায় ভোগায়।
বৃষ্টির সাথে খিঁচুড়ি খাওয়ার কি সম্পর্ক? কে, কবে এটার প্রচলন ঘটিয়েছিল জানি না। তবে, বৃষ্টির দিনে খিঁচুড়ি খাওয়া এখন আমাদের এই আটপৌড়ে বাঙালি জীবনে একরকম অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি হলেই ভ‚না খিঁচুড়ি, ডিম ভাঁজা আর ভ‚না গোশত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। মুষলধারে বৃষ্টির সময় (গ্রামে আমরা বলতাম কোপাইন্যা বৃষ্টি) ঘরের টিনের চালায় যে অপূর্ব সুরের মুর্ছনা সৃষ্টি হতো, কান পাতলে তা এখনও শুনতে পাই। নগরজীবনে সেসবের বালাই নেই। কংক্রিটের ছাদে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ঠিকই, তবে তা কোনো মোহনীয় শব্দ সৃষ্টি করতে পারে না। মনে হয় ওরা পাষাণে মাথা কুটে মরে পাইপ দিয়ে নর্দমায় নিজেদের বিসর্জন দিচ্ছে। নগরজীবনে অবশ্য বৃষ্টিকে এক অনাবশ্যক উৎপাত হিসেবেই আজকাল গণ্য করা হয়। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে বর্ষা যেন নগরবাসীর জন্য এক অভিশাপ! সামান্য বৃষ্টিতে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে অলিগলি রূপ নেয় জলাশয়ের। এই জলজটের অবশ্যাম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট দীর্ঘ সময়ের যানজট ঘর থেকে বের হওয়া কিংবা কাজ শেষে ঘরমুখো মানুষকে ফেলে অসহনীয় দুর্ভোগে। তখন আর বৃষ্টি উপভোগ্য থাকে না। তাই বলে কি বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে না? প্রকৃতি তো তার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। যে ঋতুতে যেটা হওয়া দরকার সেটা হবেই। না হলেই বরং তা অস্বাভাবিক। শীতকালে যদি শীত না পড়ে, বসন্তে যদি ফুল না ফোটে তাহলে প্রকৃতি যে তার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র দুটোই হারাবে।
আসলে আমরা যতই শহুরে বাঙালি বাবু সাজার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের শেকড় তো রয়ে গেছে কাদাপানির গ্রামে। যেখানে প্রাণ এখনও অনেকটা সজীব। যদিও নগরায়নের ছোঁয়া লেগেছে সেখানেও। তবে পুরোটা দখলে নিতে পারেনি এখনো। গ্রামে গেলে খুঁজে পাই প্রাণের সজীবতা। তাই গ্রামকে শহর বানানোর চেষ্টা না করাই বোধকরি ভালো। থাক না গ্রাম গ্রামের মতো। তাতে অন্তত কবিগুরুর ‘ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলি’ কংক্রিটের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে।
লেখক: সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক।
- সর্বশেষ খবর
- সর্বাধিক পঠিত