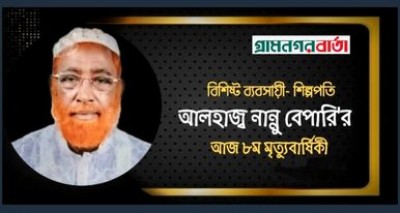পাঠ্যবই ও পাকিস্তানি মানসিকতা
 স্বদেশ রায়
স্বদেশ রায়
প্রকাশ: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ১১:০০ | আপডেট : ১৭ জুন ২০২৫, ০৫:০৪
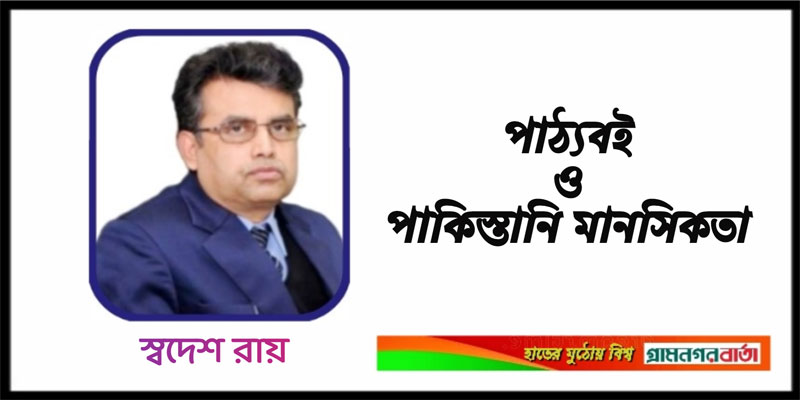
ছোটবেলায় আর দশ জন শিশুর মতো বর্ণ পরিচয়ের আগে কবিতা আবৃত্তি করার ফলে, স্কুল বই হাতে পাবার অনেক আগেই পরিচয় হয়েছিল, নজরুলের, ‘নব নবীনের গাহিয়া গান/ সজীব করিব মহাশ্মশানের’ সঙ্গে। পরে বাড়ির পণ্ডিত মহাশয় ও সেজদির কাছে শিক্ষার মাঝে একদিন স্কুলে যাবার কথা উঠলো। শুনলাম স্কুলের একটু উঁচু ক্লাসেই ভর্তি করা হবে। বইও বাড়িতে এলো। স্কুলের বইয়ে কবিতা পড়তে গিয়ে দেখি, সজীব করিব মহাশ্মশানের স্থানে ‘গোরস্থান’। সেজদির কাছে দৌড়ে বই নিয়ে গিয়ে বলি, আমাদের বাড়ির বইতে মহাশ্মশান আর এখানে ‘গোরস্থান’ কেন? তিনি অতি সাধারণভাবে বললেন, ‘পাকিস্তান তো, তাই এখন স্কুলে গোরস্থান পড়তে হবে’। সেজদির কথা সেদিন বুঝতে পারিনি কিছুই। শুধু মনে ছিল ‘পাকিস্তান তাই স্কুলের বইয়ে গোরস্থান পড়তে হবে’। এ নিয়ে মাথায় অন্য কোনও চিন্তাও আসেনি। পরে অবশ্য পাঠ্য বইয়ের এমন অনেক ‘গোরস্থানের’ সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপরে পাকিস্তানে একের পর এক পাঠ্য বইয়ে নানান বিকৃতি দেখি। এমনকি বিকৃতি দেখতে শুরু করি বাংলাদেশ হবার কিছু দিন না যেতেই।
পাঠ্য বইয়ের এই বিকৃতি যে কত ভয়ংকর একটা বিষয় এবং একটা জাতি গঠনে, মানুষ গঠনে সর্বোপরি ওই মানুষগোষ্ঠীর মনন গঠনে যে কী বিষময় ফল হয়– তা নিয়ে এ সমাজে আলোচনা খুবই কম হয়েছে। সর্বোপরি যে কাজটি হয়নি তা হলো, এই বিকৃতির একটা ইতিহাস লেখা। কারণ, একটি জাতি মননের দিক থেকে কীভাবে বিকৃত ও ধ্বংস হয়েছে তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকলে কখনোই সেখান থেকে বের হয়ে আসা যায় না। অবশ্য যদি সে ইতিহাস যারা রাষ্ট্র পরিচালক তারা পড়েন ও সেভাবে চিন্তা করেন। তবে এ মুহূর্তে না পড়লেও ভবিষ্যৎ কোনও এক প্রজন্মের জন্যে এ ইতিহাস খুবই প্রয়োজনীয়।
তথ্য প্রযুক্তির এ সময়ে বইয়ের বিজ্ঞাপনেরও ধরন ও স্থান বদলে গেছে। কয়েক দিন আগে ফেসবুকে মওলা ব্রাদার্সের একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন পেলাম। বইটির নাম ‘ ইতিহাস হত্যা এবং পাঠক্রম ও পাঠ্যবই (১৯৪৯-২০২০)’ লেখক মুনতাসীর মামুন। লেখক মুনতাসীর মামুন অবশ্য তার কিছু দিন আগে টেলিফোনে নানান বিষয় আলোচনা করার সময় বলেছিলেন, তিনি পাঠ্যপুস্তকের বিকৃতি ও ধর্মীয়করণ নিয়ে একটা বই লিখছেন। তবে সেখানে তার সব থেকে বড় অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের পাঠ্যপুস্তকের কোনও আর্কাইভ নেই। অর্থাৎ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলিয়ে গত ৭৫ বছরে দেশের পাঠ্যপুস্তক কী ছিল তা জানার কোনও পথ নেই। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার ভেতরে বসেও তিনি যে একটা ইতিহাস লিখেছেন, আর সেটা বই আকারে বের হতে যাচ্ছে দেখে অনেকটা আশ্চর্য হলাম। দ্রুতই মওলা ব্রাদার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা বই কেনার ব্যবস্থা করি। বইটিতে পাকিস্তান আমলের ও বাংলাদেশ আমলের পাঠ্যপুস্তকের বিস্তারিত ইতিহাস না থাকলেও তথ্য ও উপাদান একেবারে পরিপূর্ণ। আরও থাকতে পারতো, তবে তিনি আগেই বলেছেন, কোনও আর্কাইভ নেই। পুরনো বইগুলো পাবার কোনও উপায় নেই। তারপরেও পাকিস্তান সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার পাঠ্যপুস্তকে যে পরিবর্তন শুরু হয় আর তা নিয়ে পার্লামেন্টে যে ডিবেট হয়, পার্লামেন্টের এই প্রসেডিংস থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন অর্থাৎ বিশেষ করে ধর্মীয়করণ করার যে নগ্ন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার একটা ইতিহাস তিনি তুলে এনেছেন। শুধু তা নয়, সেখানে অতি উৎসাহী শিক্ষিত বাঙালিজন কী করেছিলেন তারও একটা ছবি পাওয়া যায়। ওই সময়ে পূর্ববঙ্গের শিক্ষার জন্যে দুটি পদ খুব বড় ছিল। এক, সচিব ও দুই, ডি.পি.আই। শিক্ষা সচিব এফ করিম ছিলেন অবাঙালি এবং ডি.পি আই ড. খুদা। যিনি বাঙালি। এই বাঙালি জনই স্কুলে স্কুলে সার্কুলার পাঠাচ্ছেন, ‘সকালে নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাসেম্বলি বা জমায়েত হবে। প্রধান শিক্ষক একজন ছাত্রকে সুরা পাঠ করতে বলবেন। তার পড়া শেষ হলে এর অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া। তারপরে কোনও সিনিয়র শিক্ষক ইসলামের ইতিহাসের কোনও গল্প বলবেন।’

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা সবসময়ই ধর্মীয় গণ্ডির ঊর্ধ্বে। সেখানে একজন বাঙালি অতি উৎসাহী হয়ে অ্যাসেম্বলিতে একটি ধর্মের অনুশাসন যোগ করে দিচ্ছেন। ভাবছেন না অন্য ধর্মের ছাত্রদের কথা। আর তার থেকে বড় হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি টেনে আনছেন ধর্মকে। এ বইয়েই দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের প্রদেশগুলোতে এমনটি ঘটছে না। এমনকি এখানে যে অবাঙালি সচিব আছেন তিনিও এতদূর যেতে চান না। আর যে ইসলামের ইতিহাসের গল্প বলার কথা হচ্ছে, সেটা আসলেই গল্প। ইতিহাস নয়। সেসব গল্প উল্লেখ করতে গিয়ে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, ‘...সুবিধামতো ফ্যাক্ট বিকৃত করা হয়েছে। যেমন- ক) ব্রিটিশরা মুসলিম শাসন উৎখাত করতে চেয়েছিল। আর তাদের সাহায্য করেছিল উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, দুর্লভ রায় ও কৃষচন্দ্রের মতো হিন্দুরা (পৃষ্ঠা-৮৯*), মীরজাফরের নোংরা বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ নেই। সিরাজউদদৌলার হিন্দু সেনাপতি মোহনলালের বিশ্বস্ততার কথাও অনুপস্থিত।’
স্কুলে এই অ্যাসেম্বলিতে সুরা পাঠসহ ইসলাম ধর্মের আরও অনুশাসন ও ইসলামের ইতিহাসের তথাকথিত গল্পগাথার বিরুদ্ধে সেদিন পাকিস্তান পার্লামেন্টে হিন্দু পার্লামেন্ট মেম্বাররা বেশ সরব ছিলেন। তারা সরকার কোথায় কী করছেন, তা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করে এসে পার্লামেন্টে অনেক উদাহরণ দিচ্ছেন। এমনকি পাকিস্তানের প্রথম কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলিতে পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে পাকিস্তানকে ধর্মীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি বা সবার রাষ্ট্র তৈরি করার কথা বলেছিলেন, সে কথাও বলছেন। আবার ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি স্কুলের শিক্ষককে এই একটি ধর্ম সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দেবার বিষয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সবার কথার ভেতর মূল সুরে কম বেশি একটা মিল আছে। সবাই যার যার নিজ নিজ ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করছেন। কেউই আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মানুষের সিভিলাইজেশনের ইতিহাস যে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া দরকার সে কথা বলছেন না।
কেন বলছেন না তা অবশ্য লেখকের এই বইতে নেই। হয়তো সেদিকে গেলে বইটি তার মূল কেন্দ্র থেকে সরে যেতো। এই মুসলিম, হিন্দু, ক্রিশ্চিয়ান সবাই নিজ নিজ ধর্মের মিথকে আঁকড়ে ধরছেন, এর মূল কারণ কিন্তু আমাদের ইতিহাসের ভিন্ন স্থানে প্রোথিত। এর শিকড় প্রোথিত রয়েছে ১৯৪৫ ও ৪৬-এর সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। যদিও এখানে তা বিস্তারিত লেখার সুযোগ নেই। তবে ৪৫, ৪৬-এর বাঙালি মানসিকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সবাই তখন কমবেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে। শুধু মুসলিম লীগ আর হিন্দু মহাসভা তখন বলছে না হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে থাকা সম্ভব না। তখন কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা শুধু নয়, তাদের থিঙ্কট্যাংক বলে যারা পরিচিত তারাও বলছেন, একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ মুসলিম লীগ ধর্মের নামে মানুষকে ভাগ করে দেশ সৃষ্টির যে উদ্ভট ধারণা দিয়েছিল, তা ততদিনে সবাই মেনে নিয়েছে– সচেতন বা অচেতনভাবে। অর্থাৎ সবাই তখন কমবেশি পাকিস্তানি মানসিকতা দিয়ে আচ্ছন্ন। আর তারই প্রকটরূপ দেখা যাচ্ছে পূর্ব বাংলায়। সেখানে পার্লামেন্টে মনোরঞ্জন গুপ্ত বলছেন, হিন্দুদের পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে দেখানো হচ্ছে।
আর এই পাকিস্তানি মানসিকতা কতটা হাস্যকর পর্যায়ে চলে গিয়েছিল তা পার্লামেন্ট মেম্বার আশালতা সেনের একটি বক্তব্য থেকে পাওয়া যায় এ বইয়ে। অ্যাডাল্ট এডুকেশনের একটা বই সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘পাখি সব করে রব রাত্রি পোহাইল/ কাননে কুসুমকলি সকলে ফুটিল্’-এর পরিবর্তে নতুন বইয়ে লেখা হয়েছে ‘ পাখি সব করে রব রাত্রি পোহাইল/ মোরগ ডাকিয়া মোর ঘুম ভাঙ্গাইল,/ ভোরের বাতাস বয় শরীর জুড়ায়/ বাগানেতে ফোটে ফুল লতায় পাতায়’। আশালতা সেন এই বিকৃত কবিতা উল্লেখ করে বেশ বড় এবং তির্যক বক্তব্য রেখেছিলেন। যার একটা লাইন এমন, ‘এর পরে মনে হয় আর বাংলার ফুল শাখাতে বুলবুলি দোল খাবে না, মোরগই সেখানে দুলবে।’
পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে বাংলার ফুল শাখাতে মোরগ দোলানের চেষ্টা থেকে পূর্ববাংলার বা পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত পাকিস্তানি মানসিকতার লোকেরা থেমে থাকেনি। থেমে থাকেনি পাকিস্তানি মানসিকতার অতি উৎসাহী বাঙালিরাও। তবে তাদের এই অতি উৎসাহের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গে সামাজিক ও মানসিক গঠনে পরিবর্তন এসে যায়। লেখক এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন।
এক. ১৯৬৯ সালের নুর খানের শিক্ষানীতিকে ঘিরে প্রফেসর এবিএম হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এক সভার আয়োজন করে। এবং সেখানে তাঁরা শুধু ২১টি সংশোধনী আনেননি, তাঁরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করা ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব আনেন। অন্যদিকে পাকিস্তান লেখক সংঘের সভার অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী স্পষ্ট করে বলেন, ‘সরকারি আমলাদের চিন্তা নায়ক বা পণ্ডিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু সৎ চরিত্রের অধিকারী হয়ে কাজ করে যাওয়া।’ অন্যদিকে নূর খানের এই শিক্ষানীতিতে ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করার দাবি বাদ দিয়ে ঐচ্ছিক করার কথা বলে বিবৃতি দেন শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, বদরুদ্দীন ওমরসহ ২৬ জন। তেমনি ‘পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি’ নামক একটি সাম্প্রদায়িক বই নবম ও দশম শ্রেণিতে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানি সরকার। জসীমউদদীন, সুফিয়া কামাল, শহীদুল্লাহ কায়সার, আহমদ শরীফ, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, ওয়াহিদুল হক, জহির রায়হান প্রমুখ ১৬ জন এই বই বাতিল করার পক্ষে বিবৃতি দেন।
এ ধরনের ঘটনা ষাটের দশকের মাঝ থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত বন্ধের সময় থেকে ঘটতে শুরু করেছে। তখন সরকারের রবীন্দ্রসংগীত বন্ধের পক্ষে থাকা অতি উৎসাহী ডি.পি আই ড.খুদার মতো বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ যেমন বিবৃতি দেন, তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষেও দাঁড়ান বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশ। ’৬৯-এ এসে দেখা যাচ্ছে, সেই বুদ্ধিজীবীরা অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতির পক্ষে ও পাঠ্যবইয়ের পক্ষে বলছেন। অর্থাৎ ৬০-এর দশকের শেষভাগে এসে পূর্ববাংলার বাঙালিদের মধ্যে ততদিনে একটি সিভিল সোসাইটি দাঁড়িয়ে গেছে। তারা সমাজের ওপর চেপে বসা এই কূপমন্ডূকতা, এই পাকিস্তানি মানসিকতার বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদদের আগেই কথা বলেছেন। বাস্তবে যখন কোনও সমাজে সিভিল সোসাইটি রাজনীতিবিদদের আগেই কোনও প্রগতিশীল দাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তখন বুঝতে হয় ওই সমাজ জীবিত ও জাগ্রত। তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আর যখন সিভিল সোসাইটি রাজনীতিবিদদের পেছনে পেছনে চলে তখন বুঝতে হবে ওই সমাজ মরণোন্মুখ। যেকোনও মুহূর্তে গভীর খাদে পড়ে যাবে সেই সমাজ।
পূর্ববাংলার এই সিভিল সোসাইটি ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধে কী কলমে, কী রাইফেল হাতে সমান তালে ছিলেন। যার ফলে স্বাধীনতা অনিবার্য হতে আরও দ্রুত গতি পায়। তবে এও সত্য, এই সিভিল সোসাইটির সদস্যদের একটি বড় অংশকে হত্যা করা হয়। আর কেন হত্যা করা হয় তাও নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে এরাই মূলত প্রগতিশীল রাজনীতির সামনে হাঁটেন। দেশকে ভবিষ্যৎমুখী করেন।
যাহোক, স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু সেই পাকিস্তান আমলের ডি.পি.আই ড. খুদা অর্থাৎ কুদরাত-ই খুদার নেতৃত্বে ২১ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, ‘এখানে অবশ্য ড. খুদার কিছু করার ছিল না। তার সেই আগের মানসিকতা প্রকাশেরও কোনও সুযোগ ছিল না। কারণ, তাকে সভায় সভাপতিত্ব করার বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল কম।’ আর সত্যি অর্থে বাস্তবতা হলো, স্বাধীন বাংলাদেশে, বঙ্গবন্ধুর আমলে শুরুতে পাকিস্তানি মানসিকতা প্রকাশের কোনও পথ ছিল না। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন শিক্ষানীতি ও পাঠ্যবই এমনই হবে– যাতে শিক্ষার মাধ্যমে তরুণ সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সামনের দিকে এগোতে পারে। ওই শিক্ষানীতি তৈরির কাজ শেষ হয় ১৯৭৪ সালে। তখন আশা করা হয়েছিল এই শিক্ষানীতির ফলে ২৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দেশে পরিণত হবে।
কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। তাই সত্যি অর্থে তার আমলে ওইভাবে কোনও পাঠ্যপুস্তক স্থায়ীভাবে রচনা হয়নি। এর পরে জিয়া ও এরশাদ আমলের শিক্ষানীতির কথাই বলেছেন বেশি লেখক। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তারা যুবসমাজকে পরিবর্তন করে ধর্মীয় পথে নিয়ে যাবার ওপর জোর দিচ্ছেন। লেখক এর পরেই চলে আসছেন ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ আমলে কবীর চৌধুরীর শিক্ষা কমিশনের বিষয়ে। এ শিক্ষা কমিশন বিষয়ে, লেখক লিখছেন, ‘এই কমিশনের অষ্টম অধ্যায় ছিল ‘ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা’ সম্পর্কিত। এর আগে কোনও কমিশনে বিস্তারিতভাবে ইসলামের কথা এত বলা হয়নি, যা এখানে বলা হয়েছে। আগের কয়েকটি কমিশনের কথা ও আরও কিছু যোগ করে এখানে বলা হয়েছে। অথচ যারা বলেছেন, তারা সকলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের।’ এখানে পাঁচ প্যারায় যা বলা হয়েছে তা পড়লে হঠাৎ কারও মনে হতে পারে এটা মূলধারার শিক্ষার নীতি না, মাদ্রাসা শিক্ষার নীতি। এরপরে দেখা যাচ্ছে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে এটা বাড়িয়েছেন। আবার ২০০৯-এ আওয়ামী লীগ এসে ২০১০ সালে যে শিক্ষানীতি দেয় তা সম্পর্কেও লেখক বলছেন, ‘ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টি আগের ৯৭-এর প্রতিধ্বনি।’
বইয়ের শেষ দিকে অনেক অংশজুড়ে আছে জনকণ্ঠ, প্রথম আলো ও ভোরের কাগজের রিপোর্ট। যেসব রিপোর্ট জানিয়েছিল হেফাজতের দাবি মেনে নিয়ে নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা লেখা শুধু বাদ দেওয়া হয়নি। ইংরেজি বইয়ের গল্পের চরিত্রের নাম উত্তম থাকায় সেটা হিন্দুয়ানি (বাংলা শব্দ নয়!) শব্দ বলে হেফাজতের দাবিতে তাকে অলিউল করা হয়। বর্তমান আমলের এই চিত্রটি তিনি এসব রিপোর্টগুলো উল্লেখ করে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।
এই যে হেফাজতের দাবি মেনে নিয়ে বাংলা শব্দ বাদ দেওয়া, বা শব্দ সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে এই যে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন হচ্ছে, আওয়ামী লীগ আমলেও যা অনেক বেশি হয়েছে। এই কাজ কিন্তু আওয়ামী লীগ মোটেই বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার হিসেবে করেনি। তারা যেমন এখন কোনও মিটিংয়ে জিয়া, এরশাদ ও খালেদার মতো সিংহাসনে বসেন, বঙ্গবন্ধুর মতো সাধারণ চেয়ারে বা ফরাশে বসেন না। এখানেও তারা জিয়া ও এরশাদের উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা নাম থাকার এবং ফুলের মালা দেবার কারণে পাঠ্যপুস্তক থেকে খালেদা জিয়ার আমলে বাদ দেওয়া হয় প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক রণেশ দাশগুপ্তের ‘মাল্যদান’ গল্প। এর মূল কারণ ছিল, গল্পের নায়ক বধ্যভূমিতে গিয়ে যে খুলি দুটিতে মালা দেয়, তারা একপর্যায়ে চিৎকার করে তাদের নাম জানায়। একজনের নাম সেতারা, আরেকজনের নাম পারুল। শেষের নামটিই ঝামেলা বাধায়। বাদ যায় গল্পটি। অবশ্য রণেশ দাশগুপ্ত নামটিও ঝামেলার। কারণ, ১৯৯২ সালে সৃজনশীল প্রকাশকদের বই মেলা উদ্বোধনীতে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অজয় রায়ের বই দেখে বলেছিলেন, ভারতীয় লেখকের বই কেন এখানে? তার কথা শুনে মফিদুল হকের মুখ লাল হয়ে যায় লজ্জায়। সাংবাদিক হিসেবে সে স্মৃতি এখনও মনে পড়ে।
এরপরে একটা বিরাট অংশজুড়ে আছে পাঠ্যবইয়ের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার চেষ্টার উদাহরণ ও জিয়াউর রহমানকে বড় করার অপচেষ্টা। এই ইতিহাস এখন সবার কম বেশি জানা। তবে পাঠ্যপুস্তকে কীভাবে থাকে এটাই প্রশ্ন। এমনকি মুজিবনগর সরকারের (বাংলাদেশের প্রথম সরকারের) ইতিহাস আছে। সেখানে জেনারেল ওসমানী ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম আছে, কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদের নাম নেই।
এই নাম না থাকার প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধুকে নানাভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টার প্রসঙ্গে গিয়ে লেখক লিখেছেন, ‘এই তিনটি বইয়ের রচনা ও সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন পরিচিত শিক্ষক। তাঁরা কেন এ ধরনের অস্বচ্ছ ইতিহাস নির্মাণ করলেন? তাহলে কি অ্যাকাডেমিশিয়ানরাও সবসময় বিদ্যমান রাজনীতিতে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন থাকেন?’
অ্যাকাডেমিশিয়ান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই রাজনীতিতে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন বা এক ধরনের আফিমের ঘোরে থাকা এবং বঙ্গবন্ধু’র মৃত্যুর পরে সব শিক্ষা কমিশনে পাকিস্তান আমলের মতো ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছেন শিক্ষাবিদরা বা বুদ্ধিজীবীরা। এর থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, রাজনীতিবিদরাও যেমন ধর্মীয় মৌলবাদীদের পেছনে হাঁটছেন শিক্ষানীতি বা পাঠ্যবই প্রণয়নের ক্ষেত্রে, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরাও তেমনি রাজনীতিবিদদের পেছনে হাঁটছেন। অর্থাৎ, ১৯৬৯-এ এসে যে সামনে চলার সিভিল সোসাইটি এই বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের একটি অংশকে ১৯৭১-এ হত্যা করা হয়; এবং আশির দশকের প্রথম অবধি ছোট আকারে হলেও অনেকে সামনের কাতারে ছিলেন, এখন তাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। সবাই রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামিযুক্ত নেতাদের পেছনে অবস্থান নিচ্ছেন।
বাস্তবে এই যে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি হেরে যাওয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তিহীন একটি সমাজ ধর্মের নামে ধর্মের ষাঁড়ের মতো স্বেচ্ছাচারীভাবে এগিয়ে চলাই মূলত পাকিস্তানি মানসিকতা। বুদ্ধিবৃত্তির পরাজয়ের এই মানসিকতা, ১৯৪৫, ৪৬-এ অখণ্ড ভারতকে গিলে খেয়েছিল। যার ফলে ধর্মের নামে দুটো দেশ হয়েছিল, মানুষের নামে নয়। বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল এই পাকিস্তানি মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসার জন্যে। কিন্তু মানসিকতা গঠন করে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার বাহন টেক্সট বইয়ের এই যখন হাল, সেখানে যখন অন্ধত্বেরই জয়ডঙ্কা, তখন তো ধরেই নিতে হবে পাকিস্তানি মানসিকতাই জেঁকে বসে আছে। আর শুধু ধর্মের কূপমণ্ডূকতা নয়, মুনীর চৌধুরী যে আমলাদের হুঁশিয়ার করে ১৯৬৯-এ বলেছিলেন, ‘ সরকারি আমলাদের চিন্তানায়ক বা পণ্ডিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন শুধু সৎ চরিত্রের হয়ে কাজ করে যাওয়া।’ আজ তারাই চিন্তানায়ক হয়ে ‘যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি’– এই কবিতার কবি আবদুল হাকিম, যার এই দুই লাইন শহীদ মিনারের সমান আকৃতির। তাঁর কবিতা পাঠ্যবই থেকে বাদ দিচ্ছে। আর এতেই বোঝা যায় শিক্ষা কোন দিকে যাচ্ছে!
লেখক: রাষ্ট্রীয় পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক
কৃতজ্ঞতায় বাংলা ট্রিবিউন।
- সর্বশেষ খবর
- সর্বাধিক পঠিত